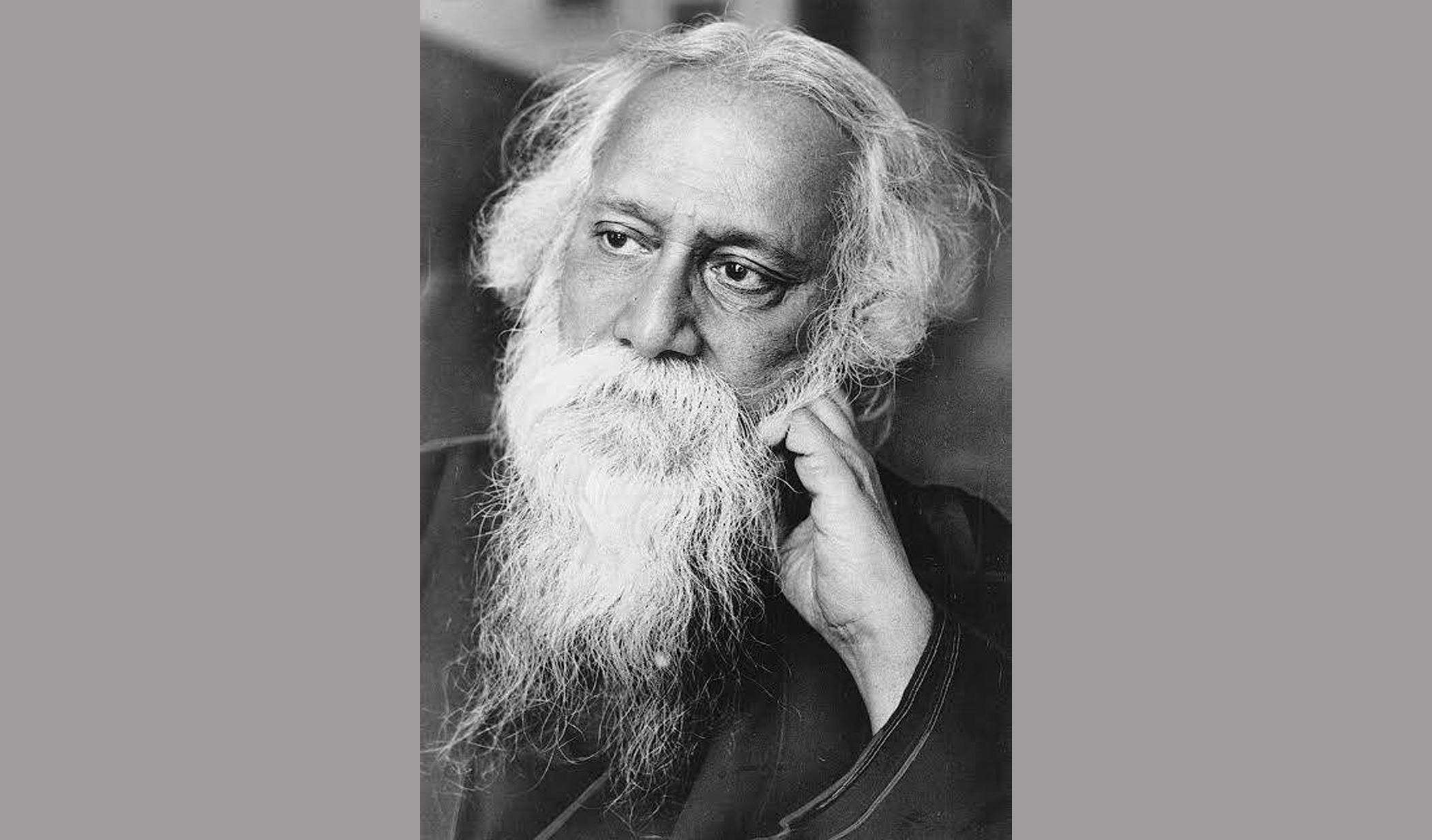
সঞ্জয় কুমার সরকার : রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে ভিয়েনায় বসে লিখছেন বনবাণী কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাংশটি। বৃক্ষের গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি এরপর লিখে চললেন এক একটি কবিতা। গাছের মধ্যে তিনি বিশ্বসংগীতের ধারা অনুভব করতেন। বিশ্বভারতীতে রোপিত গাছগুলোকে তার মনে হতো বিশ্ববাউলের একতারা। এদের পাতায় পাতায় ছন্দের নাচন।
শুধু কবিতায় নয় রবীন্দ্রনাথ প্রায়োগিকভাবে বৃক্ষাদিরোপণ ও সবুজায়নের কাজটি করেছেন। শুধু প্রকৃতিতাত্ত্বিক হয়ে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হননি, বরং কর্মের মধ্যদিয়ে তিনি প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করেছেন। নামহীন বৃক্ষ লতার নাম দিয়ে মানুষের মাঝে পরিচিত করেছেন নতুন নতুন প্রজাতিকে। শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথের বাসগৃহের সামনে বন্ধু পিয়ার্সনের দেওয়া বিদেশি চারা রোপণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একসময় এই গাছ নীল ফুলে ভরে ওঠে। নামহীন অসম্ভব সুন্দর এই ফুলটির নাম রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন ‘নীলমণিলতা’। একইভাবে ‘মধুমঞ্জরি’র বাংলা কোনো নাম সেকালে ছিল না। ফুলের রূপে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ নাম দিলেন ‘মধুমঞ্জরি’।
পূর্ববঙ্গে জমিদারী দেখাশোনার পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রামদর্শন জাগরিত হয়। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে বসবাসের এই সুযোগ এর আগে তাঁর জীবনে আসেনি। তেমনি একটি দিনে শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ যাচ্ছেন কলকাতায়। কুষ্টিয়া স্টেশনঘরের পিছনের দেয়ালে চোখে পড়ল একটি কুরচি গাছ। চারিদিকে লোকজনের হট্টগোলের মাঝে গাছ ভরে ফুটে আছে কুরচি ফুল। এই ছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কুরচির প্রথম পরিচয়। তারপর শান্তিনিকেতনে তিনি রোপণ করলেন কুরচি। অনাদারে জঙ্গলে বেড়ে ওঠা গাছ ধীরে ধীরে মানুষের সমাদরে লোকালয়ে এসে পৌঁছাল।
রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ চিন্তার অন্যতম নিদর্শন হলো বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ উৎসব। ১৯২৫ সালে কবির জন্মদিনে উত্তরায়ণে প্রথম বৃক্ষরোপণ উৎসব শুরু হয়। এরপর বৃক্ষরোপণ উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হয় বর্ষামঙ্গল উৎসব। প্রকৃতির প্রতি মানুষের দায় যে কতখানি রবীন্দ্রনাথ তা বিভিন্নভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁর লেখনী ও কর্মের মধ্য দিয়ে। ঋতুনির্ভর অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যদিয়ে কবি ঋতুব্যবস্থার সঙ্গে মানব মনের অনুভূতির প্রগাঢ় সম্বন্ধকে তিনি জাগরিত করেছেন নতুন করে। হলকর্ষণ উৎসবের মধ্যে দিয়ে সম্মানিত হয়েছিল কৃষক ও কৃষিব্যবস্থা।
নিউইয়র্কে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র লিওনার্ড এল্ম্হার্স্ট গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা ভ্রমণে গেলে এল্ম্হার্স্ট’র সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বাংলার কৃষিব্যবস্থাকে গতিশীল করতে রবীন্দ্রনাথ লিওনার্ডকে শান্তিনিকেতনে আসার আমন্ত্রণ জানান। লিওনার্ড এল্ম্হার্স্টের হাত ধরে ১৯২২ সালে সুরুল গ্রামে শুরু হয়েছিল গ্রামোন্নয়নের কাজ। রবীন্দ্রনাথ নিজ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে নিজ উদ্যোগে কৃষিবিদ্যার ওপর আধুনিক পাঠ নিতে পাঠিয়ে দেন আমেরিকাতে।
১৯০৯ সালে কৃষিবিজ্ঞানে বি.এস. ডিগ্রি নিয়ে রথীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসেন ও পিতার ইচ্ছাস্বরূপ শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনে কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। শিলাইদহে থাকতেই রবীন্দ্রনাথ গ্রামোন্নয়নের চিন্তা করেছিলেন; কিন্তু জমিদারী কাজের ফাঁকে সেটি পূর্ণাঙ্গভাবে করে উঠতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। সেই অপূর্ণ ইচ্ছারই প্রকাশ ঘটেছে শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনে। স্কটিশ নগর-পরিকল্পনাবিদ প্যাট্রিক গেডেসের (১৮৫৪-১৯৩২)-এর সঙ্গে ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। তিনি ১৯১৫ সাল থেকে প্রায় দশ বছর ভারতে নগর-পরিকল্পনার কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও প্রকৃতি পিষ্ট করে, বিপন্ন ও বিপর্যস্ত করে নগরায়ণের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরই সুযোগ্য সন্তান ড. আর্থার গেডেস (১৮৯৫-১৯৬৮) যিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন তিনি এসেছিলেন বিশ্বভারতীতে। একজন পরিবেশকর্মীরূপে আর্থার গেডেস শ্রীনিকেতনের সুরুল, রায়পুর, গোয়ালপাড়া গ্রামকে প্রকৃতিময় করে তুলতে রবীন্দ্রনাথকে সহযোগিতা করেন।
১৯২১-২২ ও ১৯২৪-২৫ এবং ১৯৩৯ সালে তিনি ভারতে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ, প্রকৃতি ও পল্লীপুনর্গঠনের ধারণা তিনি স্কটল্যান্ডে প্রচার করেছিলেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ আর্থার গেডেসকে উৎসাহিত করেছিলেন বাংলার নদীগুলোর সমীক্ষা করতে। নদীই বাংলা অঞ্চলের প্রাণ, নদী মরে গেলে গ্রামজীবনের ছন্দপতন হবে সেকথা রবীন্দ্রনাথ বহু আগে বলেছিলেন। যখন পৃথিবীতে ড্যাম নির্মাণের ধারণা জন্মেনি তখনই রবীন্দ্রনাথ মুক্তধারা নাটকে ড্যাম বিরোধী চিন্তার কথা বলেছেন। এমনকি চরাঞ্চলের জমির অধিকার সাধারণ মানুষের, কোনোভাবেই তা চাইলেই ক্ষমতালিপ্সু শাসক দখলে নিতে পারে না এই ছিল রবীন্দ্রনাথের মত। নদীতে যথেচ্ছ সেতু নির্মাণ করতে গিয়ে নদী শাসনের বিকৃত পরিবেশবিরোধী কার্যকলাপ ও শুকনো নদীতে রাস্তা নির্মাণের চরম বিরোধিতা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।
পৃথিবীতে আজ অত্যধিক জনসংখ্যার চাপ তৈরি হয়েছে। অধিক মানুষের জন্য খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এসেছে আধুনিকায়ন। কৃষি জমি বাড়াতে মরিয়া হয়ে উঠেছে মানুষ। বন-জঙ্গল উজাড় করে নির্মাণ করা হচ্ছে ঘরবাড়ি, তৈরি করা হচ্ছে কৃষিজমি। যে মানুষ একসময় বনে, গুহায় প্রকৃতির কোলে বসবাস করতো সেই মানুষ ক্রমে গ্রাস করতে থাকলো সবুজ বনভূমিকে। রবীন্দ্রনাথ এমন নির্বিচারে অরণ্যনিধনের বিরোধিতা করেছেন তার পল্লীপ্রকৃতি গ্রন্থের ‘হলকর্ষণ’ প্রবন্ধে।
‘পৃথিবীর দানগ্রহণ করবার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের। অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্র জয় করে নিলে, অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হটিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন করে। তাতে তার বাতাসকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটি উর্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব করে। অরণ্যের-আশ্রয়-হারা আর্যবর্ত আজ তাই খরসূর্যতাপে দুঃসহ।’
প্রকৃতি সহজ নিয়মে দুহাত ভরে দান করে। মানুষ ধীরে ধীরে বল প্রয়োগ করে, প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে স্বল্প সময়ে অধিক দান আদায় করে নিতে চায়। এই প্রক্রিয়া বেশিরভাগ সময়ই পরিবেশবান্ধব হয়ে ওঠে না। মানুষের লোভের সীমা এত বিস্তৃত যে তা সর্বদাই অধিক প্রত্যাশা করে। রবীন্দ্রনাথ চাষব্যবস্থা বা উৎপাদন ব্যবস্থার এই জুলুমকেও সর্বদা মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মতে যে গাছ অল্প সময়ে অতিমাত্রায় ফুল-ফলে ভরে ওঠে তা দ্রুতই নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়। আজকের আধুনিক বিশ্বে হাইব্রিড শস্য উৎপাদন ব্যবস্থার কথা রবীন্দ্রনাথের কালে ছিল না, তবুও কত সুদূরপ্রসারী চিন্তা রবীন্দ্রনাথ করতে পেরেছিলেন। এই হাইব্রিড উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষকের ঘর থেকে কেড়ে নেয়া হচ্ছে বীজ। বীজ বণ্টনব্যবস্থা এখন গুটিকতেক পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের হাতে বন্দি। যেকোনো সময় দুর্ভিক্ষ বা দুর্মূল্য তৈরি করা তাদের জন্য সহজ হয়েছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে এভাবে কিছুদূর আগানো যায়; কিন্তু শেষপর্যন্ত টিকে থাকা যায় না। এই কথাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘উপেক্ষিতা পল্লী’ প্রবন্ধে বলেছেন।
‘বর্তমানে আমরা সভ্যতার যে প্রবণতা দেখি তাতে বোঝা যায় যে, সে ক্রমশই প্রকৃতির সহজ নিয়ম পেরিয়ে বহুদূরে চলে যাচ্ছে। মানুষের শক্তি জয়ী হয়েছে প্রকৃতির শক্তির উপরে, তাতে লুঠের মাল যা জমে উঠল তা প্রভূত। এই জয়ের ব্যাপারে প্রথম গৌরব পেল মানুষের বুদ্ধিবীর্য; কিন্তু তার পিছন-পিছন এল দুর্বাসনা। তার ক্ষুধা তৃষ্ণা স্বভাবের নিয়মের মধ্যে সন্তুষ্ট রইল না, সমাজে ক্রমশই অস্বাস্থ্যের সঞ্চার করতে লাগল, এবং স্বভাবের অতিরিক্ত উপায়ে চলেছে তার আরোগ্যের চেষ্টা। বাগানে দেখতে পাওয়া যায় কোনো কোনো গাছ ফল-ফুল উৎপাদনের অতিমাত্রায় নিজের শক্তিকে নিঃশেষিত করে মারা যায়, তার অসামান্যতার অস্বাভাবিক গুরুভারই তার সর্বনাশের কারণ হয়ে ওঠে। প্রকৃতিকে অতিক্রমণ কিছুদূর পর্যন্ত সয়, তার পরে আসে বিনাশের পালা।’
কবিতায়, গানে, নাটকে, প্রবন্ধে এমনকি চিঠিপত্র ও স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথ একজন প্রকৃতিলগ্ন লেখক। সাহিত্যে প্রকৃতি-পরিবেশের বর্ণনা একটি স্বাভাবিক ঘটনা; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই প্রকৃতি ভাবনার সঙ্গে মিশে আছে প্রকৃতি বিপর্যয়ের শঙ্কা। একারণে প্রকৃতিলগ্ন কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম। কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে সচেতনতার কথা বলতে পারেন না তাই তিনি বলেন তাঁর প্রবন্ধে, নাটকে, চিঠিপত্রে। আর রবীন্দ্রনাথ কবিতায় রোমান্টিক ভাবাবেগে মিশে থাকতে চান পরিবেশ প্রকৃতির বুঁকে। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর উৎসর্গ কাব্যগ্রন্থের চৌদ্দসংখ্যক কবিতায় এই আকুতি প্রকাশ করেন-
যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই,
ধুলারেও মানি আপনা।
ছোটো বড়ো হীন সবার মাঝারে
করি চিত্তের স্থাপনা।
হই যদি মাটি হই যদি জল
হই যদি তৃণ, হই ফুলফল
জীবসঙ্গে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা।
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।
লেখক
সঞ্জয় কুমার সরকার
শিক্ষক
বাংলা বিভাগ
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়